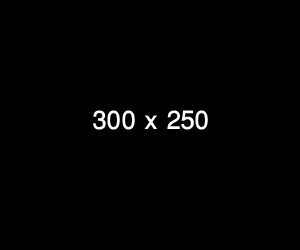মাহমুদুল হাসান উৎস
ইঞ্জিনিয়ার ও অ্যাক্টিভিস্ট
বাংলাদেশের ইতিহাসে একেকটি মাস ষড়যন্ত্রের নাম হয়ে উঠেছে—আগস্ট, নভেম্বর, আর এখন জুলাই। কিন্তু জুলাই কেবল একটি ষড়যন্ত্রের মাস নয়; এটি ছিল একবিংশ শতাব্দীর ‘সফট কুপ’-এর পাঠ্যবই। যেখানে গণআন্দোলনের ছায়ায় রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বকে হঠানো হয়, সংবাদমাধ্যমকে নিরস্ত করা হয়, এবং আন্তর্জাতিক প্রোপাগান্ডার সহায়তায় রচিত হয় এক ভুয়া গণহত্যার কাল্পনিক গাথা—যার লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় বৈধতাকে বিশ্বমঞ্চে প্রশ্নবিদ্ধ করা। এই রেড-ফ্ল্যাগ ঘটনাপ্রবাহকে ‘কোটা আন্দোলন’ বললে, তা যেমন বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, তেমনি ইতিহাসের প্রতি এক ধরণের বেইমানিও হয়ে দাঁড়ায়।
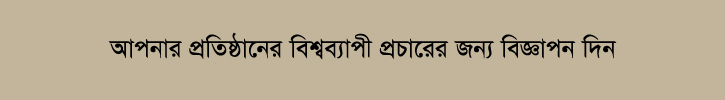
জুলাই নৈরাজ্য কেন রেড-ফ্ল্যাগ?
চলুন শুরু করি একটা মোক্ষম প্রশ্ন দিয়ে—জুলাই নৈরাজ্যে আসলে কতজন নিহত হয়েছিল?
আন্দোলনকারীরা বলছে, নিহত হয়েছে দুই হাজারেরও বেশি। এই আন্দোলনকারীদের দশা হয়েছে টিপিক্যাল পুরুষের মতন, যারা নিজের স্যালারী আর ডিক সাইজকে সবসময়ই বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করে।
জুলাইয়ে মৃত্যুর পরিসংখ্যান নিয়ে বলতে গেলে এই মুহুর্তে প্রথমেই সামনে আসবে সেই বহুল চর্চিত OHCHR-এর রিপোর্ট—যা নাকি ‘ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং’। নাম ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং, কিন্তু আসলে ফিকশন ছাপানোর কারখানা। ওই ভুয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিহত প্রায় ১৪০০ জন। এর মধ্যে পুলিশ ৪৪, আর বিজিবি-আনসার-র্যাব মিলিয়ে আরও ৮ জন।
এখন আসল প্রশ্নটা হল—এই তথাকথিত রিপোর্টকে ‘ভুয়া’ বলছি কেন?
আসুন, এবার সেই সার্কাসের পর্দা একটু তুলে দিই।
জাতিসংঘের এই রিপোর্টের দাবি এটা একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট। ভালো কথা। কিন্তু সমস্যা আরেক জায়গায়। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট নাম দিয়ে তারা তাদের রিপোর্টেই ‘বিলিভ’ বা বিশ্বাস শব্দটি ব্যবহার করেছে। আমরা আসলে কী বিশ্বাস করবো? কোনটা বিশ্বাস করবো? বিশ্বাসের প্রশ্নই বা কেনো আসছে? আমরা তো আসলে প্রকৃত সংখ্যাটা চাই, তাই না?
বিবিসি বাংলা ৩০ জুলাই প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, জুলাই মাসের সেই আন্দোলন চলাকালে, ১৬ থেকে ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে নিহতের সংখ্যা ২০৮। শিক্ষার্থীদের দাবিমতে, একই সময়ে মৃতের সংখ্যা ছিল ২৬৬। অর্থাৎ, ঘটনাক্রমে যে সংখ্যা দুই-তিনশো’র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা কীভাবে মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে ১৪০০ ছাড়িয়ে গেল, তা এক রহস্যই বটে।
আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ৮৪৩। এই সংখ্যা নিয়েও আবার বিতর্ক আছে। এক্সিডেন্টে মরা, রোগশোকে মরা—এদের কেও এই লিস্টে ঢোকানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, গাজীপুরের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীরের পিএসকে আন্দোলনকারীরা নির্মমভাবে মেরে ফেলেছিল, তাকেও জুলাই শহীদের লিস্টে রাখা হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল, এই লিস্টে মৃত সবাই আন্দোলনকারী নন, এর মধ্যে আওয়ামী লীগের অসংখ্য লোকও থাকতে পারে। আবার যশোরে জাবির হোটেল লুট করতে গিয়েআন্দোলনাকারীদের দেয়া আগুনে নিহত ১৯ জনের নাম উঠেছে এই লিস্ট।
আবার, এই লিস্টে এমন অনেকে আছে, যারা ডাকাতি করতে গিয়ে আগুনে পুড়ে মরেছে, কিংবা পিটুনিতে প্রাণ হারিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই ডাকাতদের ঠিক কোন আন্দোলনের শহীদ বলা হচ্ছে? তাদের নাম সরকারি লিস্টে কারা ঢুকালো? তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? মৃতের লিস্ট বড় করা? মিথ্যা ন্যারেটিভ তৈরি করে তৎকালীন ক্ষমতাশীনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা? এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছেও আজও অজানা।
নাটক এখানেই থেমে যায়নি, বরং এখান থেকেই শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্রের খেলা। জুলাই মাসে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে ছড়ানো হয় বিষাক্ত গুজব। উদ্দেশ্য ছিল একটাই — দেশকে অস্থিতিশীল করা, সমাজে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি ছড়ানো। বলা যায়, এই অপপ্রচারে তারা তাৎক্ষণিকভাবে সফলও হয়। তবে তামাশার বিষয় হলো, জুলাই মাসে যাদের ‘শহীদ’ বানিয়ে কাঁদানো হয়েছিল, তাদের অনেককেই আগস্টে জীবিত ফিরে আসতে দেখা যায়।
কিন্তু শুধু গুজব ছড়ানোতেই থেমে থাকেনি এই চালবাজির কারিগররা। আরও গভীরে গেলে বেরিয়ে আসে তথ্য গোপনের চিত্র।
এদিকে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হিসেবে ৮৪৩ জনের তথ্য মিললেও, OHCHR অনুযায়ী বাকি প্রায় ৫৫৭ জনের তথ্য কোথায়? এখন তো আওয়ামী লীগ নেই, ক্ষমতায় আছে আন্দোলনকারীরা। তাহলে বাকিদের লিস্ট প্রকাশে সমস্যা কোথায়? আট-নয় মাস সময় কি যথেষ্ট ছিল না? এটা নিশ্চয় ১৯৭১ সাল নয়, এটা ২০২৪ — সবার হাতে হাতে ডিজিটাল ফোন, ইন্টারনেট। তাহলে তথ্য বের করা কি সত্যিই খুব কঠিন? নাকি দায়িত্বশীলদের মধ্যে তথ্য বের করার ইচ্ছাটাই নেই?
এদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘নর্থইস্ট নিউজ‘-এর কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, প্রকৃত সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি হতে পারে। এই সংখ্যাগুলো মনে রাখবেন পাঠক। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন তাদের বিতর্কিত প্রতিবেদনে নিহতের সংখ্যা পূর্বোক্ত সরকারি ও নিরপেক্ষ উৎসের তথ্যের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। এই সংখ্যাগত বৈপরীত্য ও অতিরঞ্জন নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়: কী উদ্দেশ্যে বা কাদের স্বার্থে এমন অতিমাত্রায় মৃতের সংখ্যা বাড়িয়ে উপস্থাপন করা হলো?
এই সংখ্যাগত ভেলকিবাজি শুধু আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্রকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে না, বরং সেই সময়কার তথাকথিত ন্যায়বাদের মুখোশও খুলে দেয়। নির্লজ্জ মিথ্যাচার, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভ্রান্তি এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের গন্ধ কি এখান থেকে বেরিয়ে আসে না?
যারা নিজেদেরকে জুলাইয়ের তথাকথিত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রবক্তা বলে দাবি করে, তাদের বক্তব্য হলো—জুলাইয়ের কোনো মৃত ব্যক্তির পোস্টমর্টেম হবে না, কারও লাশ কবর থেকে তোলা যাবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন? পোস্টমর্টেম করলে কি থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়বে? কোনো নির্দিষ্ট বুলেট শনাক্ত হবে কি, যা হয়তো পাকিস্তান বা অন্য কোনো উৎস থেকে এসেছে? তাহলে কি এই আপত্তির পেছনে রয়েছে ভয়, যে সত্য প্রকাশ পেলে তাদের সাজানো নাটকের মুখোশ খুলে যাবে?
রহস্য এখানেই শেষ নয়। কারণ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একজন উপদেষ্টা, যিনি আবার জুলাই আন্দোলনের সমন্বয়কও ছিলেন, তিনি প্রকাশ্যে দাবি করেছিলেন—৫ আগস্ট সরকার পতন না হলে তারা সশস্ত্র আন্দোলনের পথে এগোতো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি সত্যিই তাই হতো, তাহলে সেই সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য অস্ত্র কারা সরবরাহ করত? কারা ছিল এই পরিকল্পনার পেছনে? এবং সেই অস্ত্র আসত ঠিক কোথা থেকে?
সবচেয়ে আশঙ্কাজনক বিষয় হলো, এই অনির্বাচিত সরকার ১৫ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত সহিংসতার জন্য দায়মুক্তি দিয়ে দিয়েছে। কেনো এই দায়মুক্তি? কাদের বাঁচাতে এই দায়মুক্তি? নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে নয়! আরও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী জানেন? এই দায়মুক্তির ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেছে জাতিসংঘের তথাকথিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট! ভাবা যায়?
থামুন পাঠক, এখনো দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানো বাকী! আমাদের কাছে এখনও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর নেই। জাতিসংঘের ওই তদন্ত কমিটি কি সেনাপ্রধান, পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) কিংবা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের সাক্ষাৎ পেয়েছিল? ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্সের (ডিএফআই) প্রধানের সঙ্গেও কি তাদের দেখা হয়েছিল? আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো—তারা কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল? যদি করে থাকে, তাহলে প্রধানমন্ত্রী তাদের কী বার্তা দিয়েছিলেন? আর যদি যোগাযোগ না করে থাকে, তাহলে কেন করা হয়নি? কার পরিকল্পনা বা নির্দেশে এই যোগাযোগ এড়িয়ে যাওয়া হলো?
একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো—জাতিসংঘের এই রিপোর্টে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি, আওয়ামী লীগের ঠিক কতজন নিহত হয়েছে। যেন ওই গ্রুপের কেউ মারা যায়নি, যেন আওয়ামী লাশ মূল্যহীন, বরং শুধু বিরোধী পক্ষের লোকজনকেই টেনে তোলা হয়েছে। অথচ দেশের ভেতরে থাকা নানা সূত্র বলছে, এই সহিংসতায় আওয়ামী লীগের বড় সংখ্যক নেতা-কর্মীও নিহত হয়েছেন। আরও অবাক করার বিষয় হলো— সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রসঙ্গও খুব ঠাণ্ডা মাথায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দায়সারা একটা অংশ রাখা হয়েছে। অথচ প্রথম আলো–র রিপোর্ট অনুযায়ী, ৫ থেকে ২০ আগস্টের মধ্যে ১,০৬৮টি সংখ্যালঘু স্থাপনায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৫০৬টি স্থাপনার মালিক আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত, আর বাকিগুলো সরাসরি সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার। তাহলে প্রশ্ন উঠছে—জাতিসংঘের রিপোর্টে কেন এতগুলো হামলাকে এড়িয়ে যাওয়া হলো?
আরেকটু গভীরে গেলে চমকের জায়গা আরও বড়। জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) জানাচ্ছে, ৫ থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে ৩৭টি হামলা হয়েছে। বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ তো ছিলই, এমনকি এক নারীকে গলা কেটে হত্যার ঘটনাও ঘটেছে। তাহলে জাতিসংঘের রিপোর্টে এসব ভয়াবহ ঘটনাকে কীভাবে নীরবে উপেক্ষা করা হলো? NSI আরও বলছে, এই হামলাগুলোর মধ্যে ৯ জন ভুক্তভোগী আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ৫টি হামলায় বিএনপি-সমর্থকদের হাত ছিল। তাহলে প্রশ্ন জাগে—এই হামলাগুলো কীভাবে শুধু বিরোধী দলের বয়ান হিসেবে তুলে ধরা হলো?
বাংলাদেশ পুলিশের পরিসংখ্যানও এই বিভ্রান্তিকে আরও স্পষ্ট করে। তাদের হিসেবে, ৪ থেকে ২০ আগস্টের মধ্যে মোট ১,৭৬৯টি হামলা হয়েছে, যার মধ্যে ১,২৩৪টি রাজনৈতিক ও মাত্র ২০টি সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দাবি আরও ভয়াবহ। তাদের মতে, একই সময়ে ২,০১০টি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা হয়েছে, যেখানে ৯ জন নিহত, ৪ জন নারী ধর্ষিত (এর মধ্যে একজন বাকপ্রতিবন্ধী), ৬৯টি উপাসনালয় আক্রান্ত হয়েছে এবং ৯১৫টি বাড়িঘর ও ৯৫৩টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও রেহাই পায়নি।
তাহলে প্রশ্ন ওঠে—OHCHR কি শুধু সরকার-নিয়ন্ত্রিত NSI আর পুলিশের তথ্য ধরে এই রিপোর্ট বানিয়েছে? যদি তাই হয়, তাহলে এই রিপোর্টের নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ করা কি অন্যায়? আরও বড় প্রশ্ন হলো, NSI আর পুলিশ তো অন্তর্বর্তী সরকারের অধীন। তাদের তথ্য কতটা খাঁটি, আর কতটা সাজানো? রিপোর্টে পক্ষপাত ঢোকানোর সুযোগ কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়?
ভালো, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের কাছেও অজানা। কিন্তু লক্ষণীয় যে, তথ্য গোপন আর ন্যারেটিভ সাজানোর এই খেলায় জাতিসংঘও নিষ্পাপ নয়।
লক্ষণীয় বিষয় হলো—বিবিসির রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকার পতনের এই আন্দোলনে হিযবুত তাহরীর সরাসরি অংশ নিয়েছিল। ৭ আগস্ট তারা সংসদ ভবনের সামনে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খিলাফতের দাবিতে পতাকা-ব্যানার নিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশ করেছে। এরপর ঢাকার বাইরে বড় বড় সভা করেছে, ‘ভারতের পানি আগ্রাসন’ বিরোধী মিছিলও করেছে। এমনকি ৯ সেপ্টেম্বর প্রেসক্লাবে গিয়ে নিজেদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবিও তোলে। তাদের মিডিয়া সমন্বয়ক ইমতিয়াজ সেলিম নিজেই জানিয়েছেন, তাদের কর্মীরা পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠনের ব্যানার ছাড়া কাজ করছিলেন, যাতে আন্দোলনটা ‘স্বতঃস্ফূর্ত’ বলে মনে হয়।
কিন্তু প্রশ্ন হলো—OHCHR-এর এই রিপোর্টে কোথায় এই হিযবুত তাহরীরের নাম? যেখানে আওয়ামী লীগ, পুলিশ আর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলার বর্ণনা পুরো রিপোর্ট জুড়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে এই জঙ্গিগোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পূর্ণ গায়েব। কেন? সাধারণ ছাত্র আর জঙ্গিদের মধ্যে যে প্রাকৃতিক বিভাজন থাকা উচিত ছিল, সেটাই কি ইচ্ছাকৃতভাবে মুছে দেওয়া হয়েছে? এতে কি এই রিপোর্ট শুধু পক্ষপাতদুষ্টই হলো না, বরং বাংলাদেশের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর ভবিষ্যৎ সহিংসতার জন্য পরোক্ষভাবে জায়গা খুলে দিল? এই রিপোর্ট কি তাহলে স্থিতিশীলতা আর নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেল?
আরও বড় বিস্ময় হলো—দেশজুড়ে যখন ইসলামপন্থীদের তাণ্ডব চলছিল, হিযবুত তাহরীরের যে উত্থান হচ্ছিল, তার কোনো হদিস নেই এই তথাকথিত ‘বিশ্লেষণধর্মী’ রিপোর্টে। কেন? অথচ ঠিক আগস্ট মাসেই শত শত জঙ্গি আর সন্ত্রাসী জেল থেকে পালিয়েছে। রিপোর্টে শুধু ১৮ জুলাইয়ের নরসিংদী জেল হামলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে—যেখানে ৮০০ কয়েদি পালিয়ে যায় আর ৮৫টি আগ্নেয়াস্ত্র লুট হয়। কিন্তু তারপর? ১৯ জুলাই থেকে আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে অন্তত ১৭টি জেলে হামলা হয়েছে, যেখানে ২,০০০-এর বেশি কয়েদি পালিয়েছে—যাদের মধ্যে ৭০ জন চিহ্নিত জঙ্গি আর ৪৩ জন শীর্ষ সন্ত্রাসী। এই ভয়াবহ ঘটনাগুলোর কথা চেপে রাখার পেছনে কার স্বার্থ কাজ করেছে? জাতিসংঘের এই রিপোর্ট কি তবে জঙ্গিদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ‘নরম মুখোশ’ তৈরির কাজে সহযোগিতা করছে?
আরও প্রশ্ন উঠছে—বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য, NSI-এর গোয়েন্দা রিপোর্ট, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভয়াবহ পরিসংখ্যান কি ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে? হিযবুত তাহরীরের মতো সংগঠনের ব্যাপক তৎপরতা যখন আন্তর্জাতিক মিডিয়া পর্যন্ত উঠে এসেছে, তখন জাতিসংঘের অফিসিয়াল রিপোর্টে তা অনুপস্থিত থাকার অর্থ কী? কারা এই তথ্যগুলো বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? তাদের উদ্দেশ্য কি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে বিকৃতভাবে তুলে ধরা?
সবশেষে আরও বড় প্রশ্ন থেকে যায়—এই রিপোর্ট কি সত্যিই মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা, নাকি নতুন করে মাঠ সাজানোর ব্লুপ্রিন্ট? এই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট তথ্যচিত্র কি বাংলাদেশকে আরও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেবে না?
গল্পের শেষ এখানেই না। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সারা দেশে ১,৪৯২টিরও বেশি ভাস্কর্য ও ম্যুরাল ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও উপড়ে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে, এই ধ্বংসযজ্ঞ কেবল ভৌত কাঠামোর বিরুদ্ধে নয়; বরং এটি ছিল একটি সুসংগঠিত সাংস্কৃতিক আক্রমণ, যার লক্ষ্য ছিল জাতির ঐতিহাসিক স্মারকগুলো মুছে ফেলা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নিদর্শন। ময়মনসিংহের শশীলজের ‘ভেনাস’, সুপ্রিম কোর্টের ‘থেমিস’, শিশু একাডেমির ‘দুরন্ত’—এগুলো কেবল শিল্পকর্ম নয়, বরং জাতির স্মৃতিচিহ্ন।
প্রথম আলোর অনুসন্ধান অনুযায়ী, মাত্র ৫ থেকে ১৪ আগস্টের মধ্যেই দেশের ৫৯টি জেলায় এই পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে। শুধু রাজধানী ঢাকাতেই ১২২টি ভাস্কর্য ও ম্যুরাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও সরকারি ভবনের অংশ ছিল। অথচ এই ভয়াবহ পরিসংখ্যান জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থার রিপোর্টে একবারের জন্যও স্থান পায়নি। রিপোর্টে মূলত শেখ হাসিনার পতনের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহিংসতা এবং আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে—কিন্তু যে সাংস্কৃতিক ধ্বংসযজ্ঞ গোটা দেশের সাংস্কৃতিক মানচিত্রকে নড়বড়ে করে দিয়েছে, সেটি সেখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত।
ফলে প্রশ্ন জাগে: এই ভাস্কর্য ধ্বংস কি কেবল ইট-পাথরের ক্ষয়ক্ষতি? মোটেও নয়। এটি আসলে জাতির সংগ্রাম, ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়কে অস্বীকার করার এক পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। বলাই বাহুল্য, প্রতিটি নিদর্শন ভেঙে ফেলার অর্থ—একটি জাতির স্মৃতিকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা। এই প্রক্রিয়া শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এটি একপ্রকার সাংস্কৃতিক নির্মূল। এমন হামলা প্রকারান্তরে মুক্তচিন্তা, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঐতিহাসিক উপলব্ধিকে ধ্বংস করে দেয়।
সেক্ষেত্রে, আরও বড় প্রশ্ন হলো—OHCHR-এর মতো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্টে এই সাংস্কৃতিক নিধনের অনুপস্থিতি কি নিছক অসতর্কতা, নাকি এটি একটি সুপরিকল্পিত এজেন্ডার অংশ? প্রশ্ন উঠতেই পারে—এই রিপোর্ট কার স্বার্থ রক্ষা করছে? কে বা কারা চাইছে যে জাতির স্মৃতি ও চেতনা বিলুপ্ত হোক, অথচ আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি যেন সেদিকে না যায়?
সবচেয়ে উদ্বেগজনক হলো—এই প্রশ্নগুলো তুললেই তা যেন অপরাধে পরিণত হয়। যদি সত্যিই মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা OHCHR-এর লক্ষ্য হয়, তবে এই ধরণের সাংস্কৃতিক গণহত্যাকে উপেক্ষা করা কি সেই আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?