শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকঃ
মুঈনুদ্দিনের মানহানি বিচার প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগী শহীদ পরিবারের সদস্যদের পক্ষ হওয়া উচিত। অবশ্য সরকারের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা ছাড়া তারা মামলার খরচ চালাতে পারবেন না। মানহানি মামলাটি হাইকোর্টে শুরু হলে এক পর্যায়ে এটি ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছার সম্ভাবনা থাকবে।
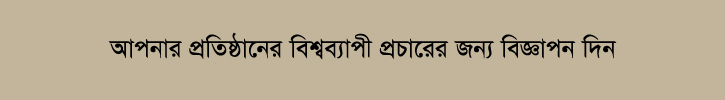
গত ২০ জুন যুদ্ধাপরাধের দায়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত, বিলেতে বসবাসকারী চৌধুরী মুঈনুদ্দিনের দায়ের করা আপিলের উপর রায় দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত, সুপ্রিম কোর্ট, যে আদালত অতীতের হাউজ অব লর্ডসের স্থলাভিষিক্ত (এরপর শুধু ‘সুপ্রিম কোর্ট’ লেখা হবে)। সে রায়ে সুপ্রিম কোর্ট এমন সব কথা বলেছেন যা বস্তুত বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করারই সামিল। আইন অঙ্গনের সঙ্গে পরিচিত নন এমন ব্যক্তিরাও জানেন যে একটি দেশের আদালত অন্য একটি সার্বভৌম দেশের আদালতের রায়ের যথার্থতা যাচাই করার অধিকার রাখেন না। এটি করা সংশ্লিষ্ট দেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপের সামিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়টি পড়ে মনে হচ্ছে সেটি যেন বাংলাদেশের আদালতসমূহের উপর কর্তৃত্ব চালানোর ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত, যে ক্ষমতা ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশ প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটির ছিল।
রায়টি শুধু অন্য একটি দেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপের সামিলই নয়, এতে রয়েছে আমাদের যুদ্ধাপরাধী বিচারের বিষয়ে অনেক ভ্রান্ত, বাস্তবতাবিবর্জিত বক্তব্য।
সুপ্রিম কোর্ট রায়ের ৬৩ প্যারাতে এমন সব কথার অবতারণা করেছেন, যা বিলেতে পড়াশুনা করা ব্যারিস্টার, সে দেশের আদালতে মামলা পরিচালনা করার, সে দেশের পররাষ্ট্র এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তাদের ট্রেনিং সেশনে পদাধিকারবলে প্রভাষকের দায়িত্ব পালন করা এবং সে দেশের একাধিক শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সটার্নাল ছাত্রদের প্রভাষক হিসাবে বহু বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট লিখেছেন, (মুঈনুদ্দিনর) মামলাটি ‘হান্টার’ মামলায় ঘোষিত নীতি থেকে আলাদা এই অর্থে যে ওই সকল মামলায় আসামিরা মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার, এবং দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অবাধ সুযোগ পেয়েছিলেন, যে সুযোগ মইনুদ্দিন পাননি। সুপ্রিম কোর্ট লিখেছেন, “অন্যদিকে আইসিটি (বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল), (মুঈনুদ্দিনর) বিচার করেছিলেন তার অনুপস্থিতিতে। বাস্তবিক অর্থে সেই মামলায় বা পরবর্তী আপিলে তার উপস্থিতি আশা করা যায় না, কেননা (মইনুদ্দিন) সত্যিকার অর্থে মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকিতে ছিলেন। (মুঈনুদ্দিনর) পক্ষে যে কৌসুলি নিয়োগ দেয়া হয়েছিল দৃশ্যত তিনি মুঈনুদ্দিনের কাছ থেকে তথ্য গ্রহন করতে হয় নারাজ ছিলেন অথবা অক্ষম ছিলেন। এটা স্পষ্ট নয় (মইনুদ্দিন) তার আপিলে কি কি হেতুবাদ প্রদান করতেন, কেননা ১৯৭৩ সালের আইন দ্বারা পদ্ধতিগত নিশ্চয়তা প্রাপ্তির অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, যেগুলো বাংলাদেশের সংবিধান এবং বাংলাদেশের ফৌজদারি কার্যবিধি দ্বারা নিশ্চিত। আইসিটি ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য গ্রহণ করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার অধিকারও তার ছিল না। তাছাড়া তিনি আপিলে সফল হলেও তার অর্থ হতো পুনর্বিচার, যাতেও তিনি উপস্থিত থাকতে পারতেন না মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার ভয়ে এবং একইভাবে তখনও সাক্ষ্য আইনের বিধানসমূহ উপেক্ষিত হতো। এ সব কারণে বলা যায় (মইনুদ্দিন) মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পূর্ণ সুযোগ পাননি।”
সুপ্রিম কোর্ট আরো লিখেছেন, “২০১৩ সালে আইসিটি প্রায় ২০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন, এবং প্রয়াত হয়েছেন এমন ব্যক্তিদের বর্ণনা বিবেচনায় নিয়েছেন। বাস্তব পরিস্থিতিতে এগুলোকে আন্দাজভিত্তিকই বলা যায়।”
সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্যের আলোকে বলতে হয় যে তারা এটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি যে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট (অতঃপর শুধু আইসিটি) নামে প্রণীত বিশেষ আইনটি ন্যুরেমবার্গ স্টেচুটের আদলেই করা হয়েছিল। বিধিমালাগুলোও ন্যুরেমবার্গ বিধিমালার অনুসরণেই করা হয়। ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের সনদ প্রণেতাগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে কিছু কিছু অপরাধী পালাতে সক্ষম হবে, আর সে বিবেচনায় ন্যুরেমবার্গ সনদের ১২ অনুচ্ছেদে প্রচ্ছন্ন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে, “কোনো আসামিকে পাওয়া না গেলে, অথবা অন্য কোনো কারণে যদি ট্রাইব্যুনাল মনে করে ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাকে বিচারের সম্মুখীন করা উচিত, তা হলে ট্রাইব্যুনাল তার অনুপস্থিতিতেই বিচার করতে পারবে।”
‘পাওয়া না যাওয়া’ বলতে সনদ নিশ্চিতভাবে এমন আসামিদের কথাই বুঝিয়েছে, যাদের গ্রেফতার করে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা যাবে না। সে অর্থে এটা বলার সুযোগ নেই যে আইসিটি আইনে আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার ব্যবস্থা ন্যায় বিচার পরিপন্থী। তদুপরি বাংলাদেশ-ভারত, কানাডা, নিউজিল্যান্ডসহ পৃথিবীর অনেক দেশের প্রচলিত আইনে আসামির অনুপস্থিতিতে বিচারের বিধান রয়েছে, কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে। আইসিটি আইনে আসামির অনুপস্থিতিতে বিচারের বিধান আমাদের প্রচলিত আইন থেকে নয়, বরং ন্যুরেমবার্গ এবং টোকিও সনদের অনুকরণে করা হয়েছে।
ন্যুরেমবার্গ সনদের প্রণেতাগণ এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে বহুল বিস্তৃত গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে অভিযোগ প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য আইনের প্রচলিত কঠোরতাকে শিথিল করা প্রয়োজন, যাতে তারা আইনের ফাঁক-ফোকর বের করে বিচার প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে না পারেন। তাই সনদের ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “ট্রাইব্যুনাল সাক্ষ্য আইনের টেকনিক্যাল বিধানসমূহ মানতে বাধ্য থাকবেন না। (ট্রাইব্যুনাল) নন-টেকনিক্যাল কার্যবিধি মেনে বিচার করতে পারবেন এবং এমন যে কোনো সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবেন, ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টিতে যার সাক্ষ্য মূল্য থাকবে।” এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্রিটিশ ব্যারিস্টার জেফরি রবার্টসন, কে সি, লিখেছেন, ন্যুরেমবার্গ সনদে ‘হিয়ারসে সাক্ষ্য’ গ্রহণের যে বিধান রাখা হয়েছিল তা এ কারণেই যুক্তিসঙ্গত যে এটি না হলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বাদ পাড়ে যেত।
সনদের ২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ট্রাইব্যুনাল সাধারণভাবে পরিচিত ঘটনার জুডিশিয়াল নোটিশ নিতে পারবেন, সরকারি কাগজপত্র এবং রিপোর্ট বিবেচনায় নিতে পারবেন।
মার্টিন বোরম্যান, ক্রুপ, যিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন এবং রবার্ট লেদের বিচার তাদের অনুপস্থিতিতে হয়েছিল (যদিও পরে জানা গিয়েছিল যে অনেক আগেই বোরম্যানের মৃত্যু ঘটেছে)। আইসিটি আইনেও সে বিধান রয়েছে, তবে তা আমাদের রাষ্ট্রীয় আইনের অনুসরণে নয়, বরং ন্যুরেমবার্গ এবং টোকিও সনদের আদলে।
১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের আইন উপদেষ্টাগণ বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন আইসিটি আইনটি বিস্তারিতভাবে বুঝে নেয়ার জন্য। বাংলাদেশে সে সময়ের কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞের সঙ্গে তারা আলোচনায় বসেছিলেন। এসব উপদেষ্টাগণ পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত গঠনের উদ্দেশ্যে যে রোম সনদ প্রণয়ন করেছিলেন তাতে অনেকাংশেই আইসিটি আইনের প্রতিফলন দৃশ্যমান। সে আদালতেও আসামির অনুপস্থিতিতে বিচারের বিধান রেখে অনুচ্ছেদ ৬১(২)(খ)-তে উল্লেখ করা হয়েছে, সকল যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টার পরেও কোনো আসামিকে পাওয়া না গেলে, তার অনুপস্থিতিতে বিচার চলতে পারে। সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য বিচারকদের ক্ষমতা প্রদান করে ৬৯(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে “আদালত যে কোনো সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা অথবা প্রাসঙ্গিকতার উপর আদেশ দিতে পারবেন এবং বিচার বিভাগীয় নোটিশ (জুডিশিয়াল নোটিশ) গ্রহণ করতে পারবেন।”
৬৯(৮) অনুচ্ছেদে এই মর্মে নির্দেশনা রয়েছে যে কোনো সাক্ষ্যের প্রাসঙ্গিকতা বা গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন বিবেচনায় আদালত সংশ্লিষ্ট দেশের রাষ্ট্রীয় বিধান অনুসরণ করবেন না।
৫২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আদালত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত মেনে সাক্ষ্য এবং কার্যবিধির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।
এরডোমভিট-এর মামলায় আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের আপিল চেম্বারের এক বিচারপতি ন্যুরেমবার্গ মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের রায়সমূহকে যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহের বিচারের জন্য মূল সূত্র হিসাবে চিহ্নিত করে বলেছেন ১৯৫০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ন্যুরেমবার্গ রায়কে উল্লেখিত বিষয়সমূহ বিচারের জন্য আইনের সূত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট বিচারপতি রবার্ট জ্যাকসন, যাকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের বিচারের জন্য তাদের শীর্ষ প্রসিকিউটর হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন, ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালে তার সূচনা বক্তব্যে বলেছিলেন, “আমরা মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার করতে না পারলে, ইতিহাস আমাদেরই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।” এই বক্তব্য দ্বারা তিনি বিশ্ববাসীকে জানাতে চেয়েছিলেন যে পৃথিবীর সকল প্রান্তেই মানবতাবিরোধীদের কঠোর বিচার হওয়া উচিত। মানবতাবিরোধী আইনে বিশ্বনন্দিত ব্যারিস্টার, জেফরি রবার্টসন, কে সি, উল্লেখ করেছেন যে ন্যুরেমবার্গ সনদ সেই গতানুগতিক তত্ত্ব থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়েছে যে আন্তর্জাতিক আইন শুধু রাষ্ট্রসমূহের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। এই সনদ নিশ্চিত করেছে আন্তর্জাতিক আইন ব্যক্তি বিশেষের বেলায়ও প্রযোজ্য যদি তারা মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করেন। ন্যুরেমবার্গ সনদ এবং সে সনদের অধীনে বিচার যে সর্বসময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক সে কথা ১৯৯৯ সালে বর্তমান সুপ্রিম কোর্টের পূর্বসুরি হাউজ অব লর্ডস পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন চিলির গণহত্যাকারী স্বৈরশাসক পিনোশের এক্সট্রাডিশন মামলার শুনানিকালে।
বিশেষজ্ঞগণ আন্তর্জাতিক ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে যে সকল অপরাধকে চিহ্নিত করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, গণহত্যা, সন্ত্রাসবাদ।
যুগোস্লাভিয়ায় গণহত্যার বিচারের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সৃষ্ট (এড-হক) ট্রাইব্যুনালের বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিরোধী অপরাধে রাষ্ট্রীয় আইন নয় বরং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন প্রয়োগ করাই সমীচীন। এর মধ্যে রয়েছে ১৯৪৮ সালের জেনোসাইড কনভেনশন এবং ১৯৪৫ সালে প্রণীত (ন্যুরেমবার্গ এবং টোকিওর) আন্তর্জাতিক মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল। ১৯৯৬ সালে ডেলালিকের মামলায় আপিল চেম্বারও একই কথা বলেছেন।
সুপ্রিম কোর্ট তাদের রায়ের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বলতে চেয়েছেন যে বাংলাদেশের আইসিটি ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়ায় বিচারকদের স্বাধীনতা, পক্ষপাতহীনতা এবং বিধিগত পরিচ্ছন্নতা ছিল না। এমন পরোক্ষ ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে আইসিটি বিচার ছিল দৃশ্যত ন্যায়নীতি বর্জিত। ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন গণমাধ্যমের, অ্যামনেস্টির, ডেমোক্রেসি ওয়াচের প্রতিবেদন দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছেন, পুরো রায় থেকে সেটি প্রতীয়মান। অথচ ১৯৯৫ সালে প্রখ্যাত সাংবাদিক জুলফিকার আলি মানিক এবং অন্যান্যরা ব্রিটিশ টেলিভিশনের জন্য যে প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করেছিলেন, তাতে প্রচুর তথ্য-উপাত্ত থাকলেও, সেগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়নি, যদিও সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সে প্রামাণ্য চিত্রের উল্লেখ রয়েছে।
আইসিটি আইনে পলাতক আসামিদের অনুপস্থিতিতে বিচারের সিদ্ধান্তের পূর্বে যে সকল শর্ত পালন করা অপরিহার্য, তার সব কটিই কঠোরভাবে পালন করা হয়েছে। স্বীকৃত মতেই মইনুদ্দিন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা পরাজিত হওয়ার পর পরই দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং ১৯৭৩ সালে বিলেতে গিয়ে সেখানে স্থায়ী হয়েছেন। আইনটি ১৯৭৩ সালে করা হলেও জিয়াউর রহমান, এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার দাক্ষিণ্য পাওয়া যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালের আগে মামলা শুরু করা হয়নি। এটা সত্য যে মামলা শুরুর প্রাক্কালে মইনুদ্দিন পূর্ব লন্ডন মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে বেশ পরিচিতি পেয়েছিলেন। সে অবস্থায় ধরে নেয়া যায় বাংলাদেশ দূতাবাসের কাছে তার ঠিকানা ছিল। ঘটনাগত ব্যাকগ্রাউন্ড শিরোনামে সুপ্রিম কোর্ট ১৬ প্যারাতে উল্লেখ করেছেন, “যুক্তরাজ্যে (মুঈনুদ্দিনর) অবস্থান জানা সত্ত্বেও তার উপর কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা সার্ভ করা হয়নি এবং তাকে মামলার কথা জানানো হয়নি। তার এক্সট্রাডিশন চেয়ে কোনো অনুরোধও করা হয়নি।” এ ব্যাপারে কারোরই ভুল করার কথা নয় যে একটি দেশের আদালতে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা অন্য একটি সার্বভৌম দেশে প্রয়োগ করা যায় না। একই প্যারাতে সুপ্রিম কোর্টের লেখা থেকে জানা যায় যে মইনুদ্দিন তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা এবং মামলার কথা জানতেন। সে বাস্তবতায় আইনের শাসনের স্বার্থে তার উচিত ছিল বিচারিক ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ গ্রহণ করার। জেনে শুনেও সেই সুযোগ না নেয়ায় অনুপস্থিতিতে তার বিচার ছিল সম্পূর্ণ বৈধ এবং যৌক্তিক। অনুপস্থিতিতে বিচার করার আগে বিদেশে অবস্থানরত কোনো আসামিকে এক্সট্রাডিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে এমন কোনো কথা কোথাও নেই। আর এক্সট্রাডিশনের অনুরোধ না করার অর্থ এই নয় যে কর্তৃপক্ষ তার উপস্থিতির ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। আমাদের দেশে অনেকের মধ্যেই এমন ভুল ধারণা রয়েছে যে ইন্টারপোলই একজন বিদেশে পালিয়ে থাকা আসামিকে ধরে ফিরিয়ে আনতে পারে। আর তাছাড়া আরও একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে এক্সট্রাডিশন চুক্তি ছাড়া বিলেত থেকে কাউকে আনা যায় না। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ পুলিশের প্রধান বলেছিলেন মইনুদ্দিনকে গ্রেফতার করার জন্য ইন্টারপোলকে অনুরোধ করা হয়েছে। তার এই বক্তব্য থেকে ধরে নেয়া যায় যে তারা ভুল ধারণা নিয়ে এই ভেবে বসেছিলেন যে ইন্টারপোল মইনুদ্দিনকে ধরে নিয়ে আসবে। সে কারণেই সম্ভবত তদন্ত সংশ্লিষ্টরা প্রাথমিক পর্যায়ে এক্সট্রাডিশন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেননি। যদিও ব্রিটিশ এবং বাংলাদেশী এক্সট্রাডিশন আইন মতে দু’দেশের মধ্যে এক্সট্রাডিশন চুক্তির প্রয়োজন নেই, তথাপিও ব্রিটিশ এক্সট্রাডিশন অ্যাক্টে বেশ কিছু কঠোর বিধান রয়েছে যার ফলে সে দেশ থেকে কোনো পলাতক আসামিকে ফিরিয়ে আনা সময়সাপেক্ষ বটে। তাছাড়া ব্রিটিশ আইনে এক্সট্রাডিশনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক ব্রিটিশ সরকার নয়, বরং ব্রিটিশ আদালত। সংশ্লিষ্ট আসামিরা হেবিয়াস করপাস মামলা করে এক্সট্রাডিশন অবরোধের চেষ্টা প্রতিহত/বিলম্বিত করতে পারেন।
বলা প্রয়োজন যে মুঈনুদ্দিনের বিচারিক ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণ দেশের অত্যন্ত মেধাবী এবং প্রজ্ঞাবান বিচারপতিদের অন্যতম। তাই এটা ধরে নেয়াই যৌক্তিক যে তাদের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল আসামির অনুপস্থিতিতে বিচারের জন্য বাধ্যতামূলক সব শর্তই কঠোরভাবে পালন করেছেন। এটিও প্রমাণিত যে ট্রাইব্যুনালের রায়ের পর ব্রিটিশ সরকারের কাছে এক্সট্রাডিশনের অনুরোধ করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল রায়ের শেষ অধ্যায়ে বাংলাদেশ পুলিশের আইজি এবং ঢাকার ডিসিকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন সাজা প্রদান করা রায়ের কপি এবং সাজা দেয়া পরোয়ানা মুঈনুদ্দিনের গোচরে আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আমার জানা মতে পুলিশ প্রধান এবং ঢাকার ডিসি ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ পালন করে রায় এবং সাজা পরোয়ানা লন্ডনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে পাঠিয়েছিলেন এবং লন্ডনে আমাদের দূতাবাসও সেগুলো মুঈনুদ্দিনের লন্ডনের ঠিকানায় যথাসময়ে পাঠিয়েছিল। সেদিক বিবেচনায় ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল করার যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ মুঈনুদ্দিনের ছিল। আপিলে মইনুদ্দিন তার বিচার পুনরায় বিচারিক ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়ে আরজি করতে পারতেন এবং আপিল বিভাগ, প্রয়োজনবোধে সে ধরনের আদেশ প্রদান করতে পারতেন। তাছাড়া আমাদের সংবিধানের ১০৪ অনুচ্ছেদ সুপ্রিম কোর্টকে পূর্ণাঙ্গ ন্যায় বিচারের জন্য সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করেছে, মইনুদ্দিন তার ব্যাপারে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্যও আপিল বিভাগে প্রার্থনা করতে পারতেন। এমন কি আমাদের সাধারণ আইনেও ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত হওয়া ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁসি দেয়া যায় না। প্রথমত হাইকোর্টের অনুমোদন ছাড়া সে দণ্ডাদেশ বাস্তবায়িত হয় না। পরবর্তীতে আপিল বিভাগে অবাধে আপিল এবং তারপর রিভিউ করা এবং সর্বশেষে রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার অধিকার পর্বগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে ফাঁসি দেয়া যায় না। আইসিটি আইনেও বিচারিক ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ডসহ যে কোনো দণ্ড প্রদান করলে তার বিরুদ্ধে দণ্ডিত ব্যক্তির অবাধ অধিকার থাকে আপিল বিভাগে আপিল করার, আপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ করার এবং সবশেষে রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার। এই প্রক্রিয়াসমূহ শেষ হওয়ার আগে কারো মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়ন করা যায় না। সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, “যৌক্তিক অর্থে এটি আশা করা যেত না যে তিনি (মইনুদ্দিন) বিচারকালে অথবা পরবর্তী আপিলে উপস্থিত থাকবেন, কেননা তিনি মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকিতে ছিলেন।” যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই সুপ্রিম কোর্টের এই মন্তব্য আইন অঙ্গনের সঙ্গে পরিচিত অনেককেই বিস্মিত করবে, কেননা তার অর্থ হচ্ছে এই যে কোনো আসামি বিচার শেষে সাজা প্রাপ্ত হতে পারেন ভেবে তার অধিকার রয়েছে বিচারিক বা আপিল আদালতে উপস্থিত না হওয়ার। সুপ্রিম কোর্ট ১৩ প্যারাতে ব্যক্ত করেছেন যে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে এমন পরিবর্তন আনা হয়েছে যার ফলে আসামিদেরকে ট্রাইব্যুনালের গঠন এবং এগুলোর সদস্যদের নিয়োগ চ্যালেঞ্জ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রচলিত ফৌজদারি কার্যবিধি এবং সাক্ষ্য আইনের প্রয়োগ বাস্তবায়িত করতে চাওয়ার অধিকার থেকে এবং মৃত্যুদণ্ড রোধ করতে চাওয়ার অধিকার খর্ব করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের উল্লেখিত মন্তব্য সত্যিকার অর্থে বিস্ময়কর। যুক্তরাজ্য এবং পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশেই আসামিদের এমন কোনো অধিকার দেয়া হয়নি যে তারা আদালতের গঠন, বিচারকদের নিয়োগ চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে ফৌজদারি কার্যবিধি এবং সাক্ষ্য আইনে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি এবং এ বিষয়সমূহে আসামিদের কোনো অধিকারই সংকুচিত করা হয়নি। আইসিটি আইনে বলা হয়েছে যে যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালগুলো দেশের প্রচলিত সাক্ষ্য আইন এবং কার্যবিধি মানতে বাধ্য থাকবেন না। ন্যুরেমবার্গ এবং টোকিও সনদের অনুকরণেই এ ধরনের বিধান করা হয়েছে। একইভাবে সংবাদপত্রের রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের বিধানও সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে করা হয়নি, তাও করা হয় আদি আইসিটি আইন মোতাবেক, ন্যুরেমবার্গ এবং টোকিও ট্রাইব্যুনালের অনুসরণে। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেও সর্বোচ্চ সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে সংশোধনের দ্বারা বিচারিক ট্রাইব্যুনাল এবং আপিল বিভাগ থেকে আসামিদের ন্যায়বিচার পাওয়ার কোনো অধিকারই খর্ব করা হয়নি। আইসিটি আইনে এবং সে অনুযায়ী প্রণীত বিধি বিধানে বিচার প্রক্রিয়ায় অন্যান্য আইনের আসামিদের মতো যুদ্ধ অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরও নিরঙ্কুশ অধিকার দেয়া হয়েছে পছন্দের আইনজীবী নিয়োগের, সাক্ষী ডাকার, প্রসিকিউশন সাক্ষীদের জেরা করার, যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের। আসামিগণ দিনের পর দিন বিনা বাধায় প্রসিকিউশনের স্বাক্ষীদের জেরা করেছেন, বিলেতে পড়াশুনা করা এক চৌকস ব্যারিস্টারসহ বেশ কয়েকজন আইনজীবী আসামিদের পক্ষে কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেছেন, যারা ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল ছাড়াও যুগোস্লাভ, রুয়ান্ডার এড-হক ট্রাইব্যুনাল এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ নজির হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। ‘সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে বিচারিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সেই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ যোগ্য নয়’– সুপ্রিম কোর্টের এমন কথা মোটেও ঠিক নয়। প্রতিটি সাজাপ্রাপ্ত আসামিরই অখণ্ডণীয় অধিকার ছিল/আছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত, আপিল বিভাগে আপিল করার। আপিলে দণ্ডাদেশ এবং সাজার মেয়াদ, উভয়কেই চ্যালেঞ্জ করা যায়। ঘটনাগত এবং আইনগত উভয় দিক পর্যালোচনার ক্ষমতা, এবং সর্বোপরি পূর্ণাঙ্গ ন্যায় বিচারের ক্ষমতা আপিল বিভাগের রয়েছে বিধায় সে বিভাগ যদি দেখতে পান বিচারিক ট্রাইব্যুনাল সাক্ষী গ্রহণের ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা হলে আপিল বিভাগ তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে, এমনকি মামলাটি পুনরায় বিচারের জন্য বিচারিক ট্রাইব্যুনালে ফেরত পাঠাতে পারেন। তাছাড়া ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিজস্ব সিদ্ধান্ত রিভিউ করারও বিধান রাখা হয়েছে। আমাদের ফৌজদারি কার্যবিধিতে ৫৬১-ক ধারায় যেভাবে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগের সহজাত ক্ষমতাকে অক্ষত রাখা হয়েছে, একইভাবে যুদ্ধাপরাধী বিচার ট্রাইব্যুনালগুলোকেও একই ধরনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।
আসামিগণ যাতে বার বার বিনা কারণে জুডিশিয়াল রিভিউর মামলা করে যুদ্ধাপরাধ মামলা বিলম্বিত করতে না পারেন, সে উদ্দেশ্যেই ১৯৭৩ সালে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি কমিশন যুদ্ধ অপরাধের অভিযোগে জাপানি জেনারেল ইয়ামাশিতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলে তিনি পর্যায়ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে এই দাবি করে হেবিয়াস করপাস মামলা করেছিলেন যে তাকে বিচার করার কোনো এখতিয়ার মিলিটারি কমিশনের ছিল না। কিন্তু মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এছাড়াও কন্ট্রোল কাউন্সিলের ১০ নং আইন মোতাবেক ন্যুরেমবার্গে যুক্তরাষ্ট্র যে সকল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল (ন্যুরেমবার্গের মূল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল থেকে আলাদা) তাদের দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত কয়েকজন আসামিও ট্রাইব্যুনালগুলোর এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ করে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে জুডিশিয়াল রিভিউর মামলা করলে যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্ট তাদের আবেদন নাকচ করে দিয়েছিলেন।
আসামির অনুপস্থিতিতে বিচারের স্বীকৃতি
লেবাননের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ইভানা হার্ডলিকোভা বলেছিলেন, “আন্তর্জাতিক ফৌজদারি বিচারের মূল মন্ত্র অপরাধীদের সাজা দেয়ার চেয়েও বেশি। আসামিদের অনুপস্থিতিতে বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এমন সুযোগ দেয়া যাতে তারা মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্তদের যথাযোগ্য বিচার নিশ্চিত করতে পারেন।” ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আইনজীবীদের একাধিক আন্তর্জাতিক সমিতি ২০১৬ সালের জুন মাসে হ্যাগ শহরে অনুপস্থিত আসামিদের বিচার বিষয়ে যে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিল, তাতে মূল প্রবন্ধকার হিসাবে লেবানন বিশেষ আদালতের উল্লেখিত প্রেসিডেন্ট উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। বৈঠকে ব্যারিস্টার জেফরি রবার্টসন, কেসিসহ যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, গণহত্যা প্রভৃতি আইনে বিশেষজ্ঞ বেশ কয়েকজন আইনজ্ঞ ও আইনের অধ্যাপক বক্তব্য রেখেছিলেন। অনেকে বলেন আসামির অনুপস্থিতি বিচারের পেছনে মূল যুক্তি হলো আসামি যাতে পালিয়ে যেয়ে বিচার প্রক্রিয়া ব্যর্থ বা বিলম্বিত করতে না পারেন। বিচারহীনতা রোধের সংস্কৃতি রোধেও এটি ভূমিকা রেখে থাকে, যা আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইনের উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন। অনেক বক্তা বলেছেন পলাতক আসামিদের বিচার না করার কারণে জনমনে এমন আশঙ্কা জাগতে পারে যে পালিয়ে থাকাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে, পালিয়ে থাকাই শ্রেয়। তাছাড়া ভুক্তভোগীদের স্বার্থেও অনুপস্থিত আসামিদের বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। বলা হয়েছে যদি হাজির হওয়ার সুযোগ সত্ত্বেও আসামি হাজির না হয়, সে ক্ষেত্রে, অনুপস্থিতিতে বিচারের ঐচ্ছিক ক্ষমতা (discretion) আদালতের থাকা উচিত। আলোচনায় ফরাসি দেশের কোর্ট অব আপিলের এক সিদ্ধান্তের কথা উঠে আসে যাতে ১৯৭৩ সালে চিলিতে গুম করার অপরাধে ফরাসি আদালত গুম কার্যে অভিযুক্তদের অনুপস্থিতিতে বিচার করেছিলেন, কূটনৈতিক মাধ্যমে অভিযুক্তদের বিচারের দিন তারিখ জানানোর পরেও আসামিগণ আদালতে হাজির হননি। এই আদেশে ভুক্তভোগীগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। ন্যুরেমবার্গে মার্টিন বোরম্যানের বিচার অনুপস্থিতিতেই হয়েছিল। কম্বোডিয়া এবং সিয়েরা লিওনের বিশেষ আদালতেও আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার করা যায় যদি আসামি মামলার শুরুতে হাজির হলেও পরবর্তীতে আত্মগোপনে যায়। ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের বিধি পরিবর্তন করে আসামিদের অনুপস্থিতিতে বিচারের ব্যবস্থা করার আগে কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি মুইগাই কেনিয়াত্তার অনুপস্থিতিতে বিচার অনুমোদন করা হয়েছিল। লেবাননের মানবতাবিরোধী অপরাধ বিষয়ক বিশেষ আদালতে (STL) আসামির অনুপস্থিতিতে বিচারের বিধান রয়েছে। ইউরোপীয় মানব অধিকার কোর্ট ব্যক্ত করেছেন, আসামিদের অধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করার পর, তাদের অনুপস্থিতিতে বিচার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিধানাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।
প্রসিকিউটার বনাম মেহরি মামলায় লেবানন ট্রাইব্যুনাল উল্লেখ করেছিলেন যে আসামি মামলার ব্যাপারে অবগত ছিলেন বিধায় এটা ধরে নেয়া যায় যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বিচার এড়াচ্ছিলেন। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ফর লেবানন, যুগোস্লাভিয়া এবং রুয়ান্ডায় মানবতাবিরোধী অপরাধীদের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সৃষ্ট এড-হক ট্রাইব্যুনপালগুলোতেও ক্ষেত্র বিশেষে আসামির অনুপস্থিতিতে বিচারের বিধান রয়েছে।
হিউম্যান রাইটস কমিশনের (এইচআরসি) বক্তব্য হলো এই যে তার বিচার হবে, আসামিকে এমনটি জানানোর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের থাকলেও তাদের প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতাকেও স্বীকার করা প্রয়োজন।
সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকে পরিষ্কার যে মাননীয় বিচারপতিগণ অনেক কিছু না জেনেই রায় দিয়েছেন এবং যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞ ব্যারিস্টার এন্থনি হাডসন কে, সি, সুপ্রিম কোর্টে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দাখিল করতে পারেননি। তিনি বাংলাদেশের কারো কৌসুলি ছিলেন না, কৌসুলি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের। কিন্তু এই মামলায় ব্রিটিশ সরকার এবং বাংলাদেশের ভুক্তভোগী মানুষদের স্বার্থ অভিন্ন বিধায় তার উচিত ছিল বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য, এবং বিশেষ করে আইসিটি আইন, তার প্রয়োগ, আপিল প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে জেনে নেয়া। দূতাবাস উপদেশ দেয়ার অবস্থানে ছিল না ঠিকই, কিন্তু কোথায় এবং কাদের কাছ থেকে উপদেশ নেয়া যায় তা জানাতে পারত।
সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন বাংলাদেশ মুঈনুদ্দিনের এক্সট্রাডিশনের চেষ্টা করা হয়নি। কথাটি মোটেও ঠিক নয়। বিচার প্রক্রিয়া শুরুর আগে এক্সট্রাডিশনের অনুরোধ করা না হলেও, রায়ের পর ২০১৪ সালে বাংলাদেশ মুঈনুদ্দিনের এক্সট্রাডিশন চেয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিল, এ কথাও ব্রিটিশ সরকারের ব্যারিস্টার সুপ্রিম কোর্টকে জানাননি। সম্ভবত তিনি একথা জানতেনও না। বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধী বিচারিক ট্রাইব্যুনালে এবং পরবর্তীতে আপিল বিভাগে যে ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা ছিল, সে কথাও তিনি সুপ্রিম কোর্টকে বুঝাতে পারেননি। তিনি এটাও বুঝাতে পারেননি যে বিচারগুলো সাধারণ অপরাধের বিচার নয়, বরং গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, যে সব অপরাধের বিচার দেশের সাধারণ আইনে হয়নি, বরং বিশেষভাবে প্রণীত আইনে হয়েছে, ন্যুরেমবার্গ ও টোকিও সনদের অনুকরণে। পরবর্তীতে যুগোস্লাভিয়া, রুয়ান্ডা, কম্বোডিয়া প্রভৃতি এলাকায় মানবতাবিরোধী অপরাধকারীদের বিচারের জন্য এবং পৃথিবীময় এসব অপরাধের বিচারের জন্য ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত গঠন করা হয়েছে এ বিবেচনায় যে হেন মারাত্মক অপরাধগুলো থেকে যেন মানব জাতিকে রক্ষা করা যায়। আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞগণ এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এ ধরনের আসামিদের বিচারের জন্য গতানুগতিক পদ্ধতি পরিহার করে বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। ব্রিটিশ সরকারের ব্যারিস্টার বোঝাতে সক্ষম হননি যে এসব অপরাধীদের বিচারের জন্য গতানুগতিক সাক্ষ্য আইন এবং কার্যবিধি শিথিল করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে আমাদেরও ভুল অস্বীকার করার সুযোগ নেই। আমাদের উচিত ছিল মইনুদ্দিন যে সকল বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে তাদের পোষ্যদের ব্রিটিশ মামলায় পক্ষভুক্ত করার চেষ্টা করা। সে চেষ্টা সফল হলে তাদের পক্ষে এমন কোনো খ্যাতনামা ব্যারিস্টার নিয়োগ সম্ভব হতো যিনি মানবতাবিরোধী অপরাধ আইন ও বিচারে সিদ্ধহস্ত। তাছাড়া ওই ব্যারিস্টারকে আমরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং তথ্যউপাত্ত প্রদান করতে পারতাম, যেগুলো ব্রিটিশ সরকারের ব্যারিস্টারকে, সে না চাওয়ায় দেয়ার সুযোগ ছিল না। তবে মামলা চালিয়ে যাওয়া খুবই ব্যয়বহুল হতো বিধায় ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের পক্ষে তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না, আর তাই এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা ছিল অপরিহার্য। অনেকেই বলছেন বাংলাদেশ সরকারের উচিত ছিল সুপ্রিম কোর্টে একজন ব্যারিস্টার নিয়োগ দেয়া। বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে তারা পরিচিত নন বলেই এ ধরনের ভুল কথা বলছেন। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কোনো আদালতেই তার কৌসুলি নিয়োগ দিতে পারেন না, তিনি সেই মামলায় পক্ষ না থাকলে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকার ওই মামলায় কোনো পক্ষ ছিল না, তাই তাদের পক্ষে কোনো ব্যারিস্টার নিয়োগ করার কোনো সুযোগ ছিল না।
এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা বিশ্ববাসীর কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে এ থেকে পরিত্রাণের পথ কি? মন্তব্যগুলো ব্রিটিশ সরকারের নয় বরং ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আদালতের। এগুলো ব্রিটিশ সরকারের ভাষ্য হলে বাংলাদেশ সরকার তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করে তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করতে পারত। কিন্তু ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্টের কাছে তো আর এ ধরনের প্রতিবাদ করার সুযোগ নেই, আর প্রতিবাদ করলেই যে সুপ্রিম কোর্ট তাদের রায় পাল্টিয়ে দেবে, তাও নয়। এ রায়ের ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন এটি প্রমাণ করা যে ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্ট ভুলের আশ্রয় নিয়েছেন। ব্রিটিশ সর্বোচ্চ আদালত, অর্থাৎ অতীতের হাউজ অব লর্ডস যে একাধিকবার ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, তার নজির রয়েছে। বিশেষ করে হাউজ অব লর্ডস ১৯৮০ সালে জামিরের মামলায় যে রায় দিয়েছিলেন তার চার বছর পরই ১৯৮৪ সালে খাওয়াজার মামলায় ঠিক উল্টো সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। বর্তমান রায়টি নিম্ন আদালতের হলে উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের ভুল সংশোধন করতে পারতেন, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের উপরতো যুক্তরাজ্যে আর কোনো আদালত নেই। ১৯৫০ সালের ইউরোপীয় কনভেনশন অন হিউম্যান রাইটসের ধারাবাহিকতায় ইউরোপীয় কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস নামে যে আদালত রয়েছে, সে আদালতের প্রয়োগ ক্ষমতা না থাকলেও তার মতামত গুরুত্বপূর্ণ। সেই আদালতে মামলা করতে হলে দেখাতে হয় যে ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশনে উল্লেখিত কোনো বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার এ ধরনের কিছু দেখাতে পারবেন বলে মনে হয় না বিধায় ইউরোপীয় হিউম্যান রাইটস আদালতে যাওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। বাংলাদেশী ভুক্তভোগীরা সুপ্রিম কোর্টের বিচারে কোনো পক্ষ ছিলেন না বলে তাদেরও সুযোগ নেই ইউরোপীয় হিউম্যান রাইটস আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার। ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে বিচারিক আদালত রয়েছে, সেখানেও যাওয়ার সুযোগ নেই কেননা যুক্তরাজ্য এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য নয়। অনেকে মনে করছেন মইনুদ্দিন তার মানহানি মামলা হাইকোর্টে শুরু করলে মইনুদ্দিন যাদের হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে তাদের স্ত্রী-সন্তানগণ সেখানে পক্ষভুক্ত হয়ে, নিজস্ব ব্যারিস্টারের মাধ্যমে আমাদের কথাগুলো ব্যক্ত করতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় সাক্ষী সাবুদ উপস্থাপন করতে পারবেন। আমিও তাদের সঙ্গে একমত। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে এফিডেভিটের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সাক্ষ্য গ্রহণ না করে। কিন্তু হাইকোর্টে মূল মানহানি মামলার শুনানি হলে তখন সেখানে সাক্ষী গ্রহণ এবং পর্যালোচনার সুযোগ থাকবে বিধায় হাইকোর্ট, নিশ্চিত হলে এমন রায় দিতে পারবেন যে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধী আইন এবং সে আইনের অধীনে বিচার ব্যবস্থায় ন্যায় বিচার তত্ত্বের কোনো ত্রুটি ছিল না, ন্যুরেমবার্গ ও টোকিও ট্রাইব্যুনালের আদলেই আইনটি হয়েছে, এবং বিচার হয়েছে, গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য যা প্রয়োজন ছিল। হাইকোর্ট এই ধরনের কথা ব্যক্ত করে কোনো রায় প্রদান করলে, তা ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে কিনা তা একটি প্রশ্ন বটে। যুক্তরাজ্যের কোনো আদালতই তাদের সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে সাংঘর্ষিক রায় দিতে পারে না। কিন্তু এখানে কথা থাকবে এই যে সুপ্রিম কোর্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন এফিডেভিটের ভিত্তিতে, সাক্ষ্যগ্রহণ না করে, যেগুলোকে আইনের ভাষায় ‘রেসিও ডেসিডেন্ডি’ (অবশ্যই অনুসরণযোগ্য) বলা নাও যেতে পারে। অপরদিকে হাইকোর্ট রায় দেবে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। তাই মুঈনুদ্দিনের মানহানি বিচার প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগী শহীদ পরিবারের সদস্যদের পক্ষ হওয়া উচিত। অবশ্য সরকারের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা ছাড়া তারা মামলার খরচ চালাতে পারবেন না। মানহানি মামলাটি হাইকোর্টে শুরু হলে এক পর্যায়ে এটি ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছার সম্ভাবনা থাকবে। মুঈনুদ্দিনের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত মন্তব্য পরিবর্তনের জন্য কিভাবে, কি পন্থা অবলম্বন করা যায়, সেটি নিঃসন্দেহে অনেক চিন্তার এবং গভীর গবেষণার বিষয়। এ ক্ষেত্রে হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ নেই, যে কথা আমি সম্প্রতি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে বলেছি। ব্রিটিশ আইন এবং বিচার ব্যবস্থায় যাদের গভীর জ্ঞান রয়েছে, যারা ব্রিটিশ আদালতসমূহে মামলা পরিচালনা করেছেন এবং পাশাপাশি বাংলাদেশের আইসিটি আইন এবং বিচারের ব্যাপারে যাদের নিরঙ্কুশ জ্ঞান রয়েছে, অর্থাৎ সে প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন, এমন ব্যক্তিদের থেকে পরামর্শ নেয়া অপরিহার্য। এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক না হলেও, কিছুতো নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং সব কিছু গভীরভাবে বিবেচনা ও চিন্তা করেই আমাদের এগুতে হবে।
(বিডি নিউজ ২৪ এর সৌজন্যে)







